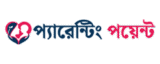যে ৭টি ভুলের জন্য অধিকাংশ বাবা-মা পরে আফসোস করেন
পিতামাতা হওয়া মানেই কেবল খুশির রোলার কোস্টারে চড়া নয়—এটি এমন একটি যাত্রা, যেখানে প্রচুর চড়াই-উৎরাই, ভুল এবং আফসোস জড়িয়ে থাকে। প্রায় সব বাবা-মা-ই সন্তানদের জন্য সবচেয়ে ভালোটা চান, কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় সম্ভব হয় না। ভুল হতেই পারে—কারণ, আমরা সবাই মানুষ। তবে কিছু ভুলের খেসারত অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়, যা পরে আফসোসে পরিণত হয়। বিভিন্ন বাবা-মার নিজস্ব নীতি ও মূল্যবোধ থাকলেও একটি বিষয়ে সবাই একমত—যদি সময়কে ফিরিয়ে নেওয়া যেত, তাহলে অনেকেই কিছু ভুল শুধরে নিতে চাইতেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক কি সেই ৭টি সাধারণ ভুল যার জন্য অধিকাংশ বাবা-মা পরে আফসোস করেন। ১. সন্তানের সঙ্গে পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাব জীবনের ব্যস্ততায় আমরা প্রায়শই সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় পাই না। ছোট বাচ্চারা হয়তো ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, তবে তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, কথা বলা, হাসা-কান্না ভাগ করে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন একটু সময় আলাদা করে সন্তানকে মন দিয়ে শোনা ও কথা বলা আপনার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলে। অনেক বাবা-মা যখন বুঝতে পারেন যে সন্তান বড় হয়ে গেছে, তখন তারা আফসোস করেন—কেন আরও সময় দিলাম না! ২. আদর করে বুকে জড়িয়ে না ধরা কে না চায় ভালোবাসার আলিঙ্গন? হ্যাঁ, একটু জড়িয়ে ধরা, একটু আদর, সন্তানের মনে নিরাপত্তা ও ভালোবাসার অনুভব তৈরি করে। জড়িয়ে ধরলে শরীরে “হ্যাপি হরমোন” বা আনন্দদায়ক হরমোন নিঃসরণ হয়, যা মন ভালো রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু অনেক সময় বাবা-মা ব্যস্ততা কিংবা সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে সন্তানের প্রতি এই ছোট্ট ভালোবাসার প্রকাশটুকুও করতে ভুলে যান। মনে রাখবেন—যখন সন্তান একটু বড় হয়ে যাবে, তখন হয়তো ওরা নিজেই দূরে সরে যাবে। তাই যতটা পারেন, এখনই আলিঙ্গন করে নিন! ৩. মুহূর্তগুলো ধরে না রাখা আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করি—ছবি তোলা, ভিডিও করা এখন আর কষ্টকর কাজ নয়। তবুও আমরা অনেকেই ভাবি—পরে তুলব, এখন দরকার নেই। কিন্তু এই “পরে” বলতেই কত স্মৃতি হারিয়ে যায়। ছোট ছোট মুহূর্ত, যেমন শিশুর প্রথম হাঁটা, প্রথম কথা বলা, জন্মদিনের হাসি—এসব ক্যামেরাবন্দি করে রাখুন। একদিন যখন স্মৃতির পাতায় ফিরে তাকাবেন, তখন এই মুহূর্তগুলোই হবে অমূল্য। ৪. সৃজনশীল খেলার সুযোগ না দেওয়া শিশুরা জন্মগতভাবে কল্পনাশক্তিতে ভরপুর। তারা যখন খেলাধুলায় মেতে ওঠে, তখন তাদের মস্তিষ্কে নতুন নতুন চিন্তার সঞ্চার হয়। অনেক বাবা-মা শুধু নির্দিষ্ট, “শেখার” মতো খেলাতেই শিশুদের সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু আপনি কি জানেন—যখন শিশুকে স্বাধীনভাবে আঁকতে বা গড়তে দেওয়া হয়, তখনই সে নিজের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে? তাদের আঁকা ছবির ভুল ধরবেন না, বরং উৎসাহ দিন। এভাবেই শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ৫. অতিরিক্ত কঠোর হওয়া “বেশি নিয়মে বাঁধা থাকলে সন্তানরা ভালো হয়”—এই বিশ্বাস এখনও অনেক বাবা-মার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ কিংবা কড়াকড়ি সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। অনেক সময় সন্তানেরা মিথ্যা কথা বলতে শুরু করে শুধুমাত্র শাস্তি এড়ানোর জন্য। কঠোর শাসনের বদলে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, তাহলে সন্তান আপনার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলবে। পরে যখন সন্তানেরা দূরে সরে যায়, তখন বাবা-মার মনে কেবলই আফসোস থেকে যায়—“আমি কেন এত কঠোর ছিলাম?” ৬. সন্তানের মতামতকে অবমূল্যায়ন করা আমরা প্রায়ই মনে করি—আমরা বড়, তাই সবকিছু আমরাই ভালো বুঝি। কিন্তু সন্তানেরাও চিন্তা করতে পারে, তাদের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। সন্তান যখন কিছু বলতে চায়, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। শুধু উপদেশ না দিয়ে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিন। এতে তাদের আত্মমর্যাদা বাড়বে এবং আপনি হয়তো তাদের কাছ থেকেও কিছু শিখতে পারেন। ৭. অর্থ উপার্জনের চাপে স্মৃতিগুলো বানানো হয়ে ওঠে না পরিবারের জন্য পরিশ্রম করা জরুরি, কিন্তু সেই সঙ্গে সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানোও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। একটা জরুরি মিটিং একদিন পিছিয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু সন্তানের সঙ্গে পার্কে যাওয়া, একসাথে গল্প শোনা বা পিকনিকে যাওয়া—এসব স্মৃতিই একদিন অমূল্য হয়ে উঠবে। সন্তানের চোখে শৈশব মানেই হবে ভালোবাসা আর আনন্দে ভরা মুহূর্ত, যদি আপনি পাশে থাকেন। পিতামাতা হওয়া কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা ম্যানুয়াল অনুযায়ী চলে না। সব চেষ্টার পরেও কিছু না কিছু ভুল হতেই পারে। কিন্তু নিজেকে দোষারোপ না করে, নিজের সন্তানকে ভালোবেসে, বোঝাপড়া তৈরি করে আগানোই হলো সঠিক পথ। যদি আপনি সন্তানের সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন—যেখানে ভালোবাসা, সম্মান আর বোঝাপড়া রয়েছে—তাহলে আপনি সত্যিই একজন সফল পিতা-মাতা।
যে ৭টি ভুলের জন্য অধিকাংশ বাবা-মা পরে আফসোস করেন Read More »